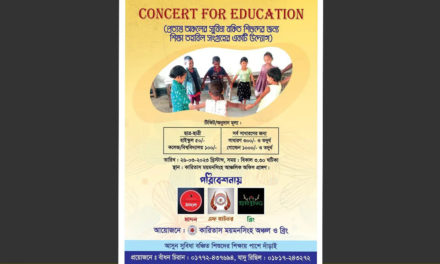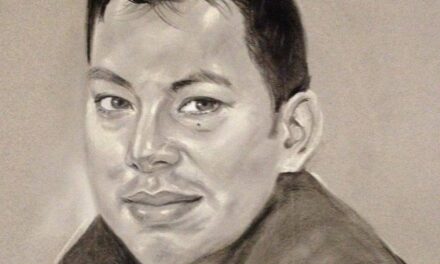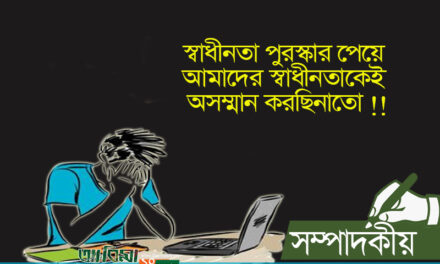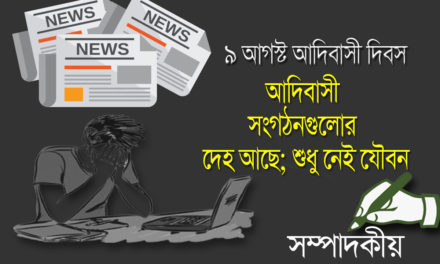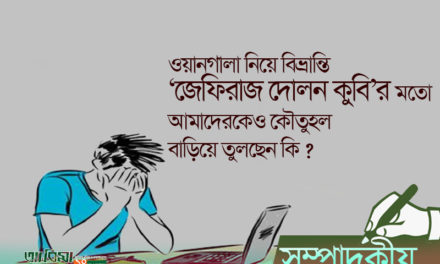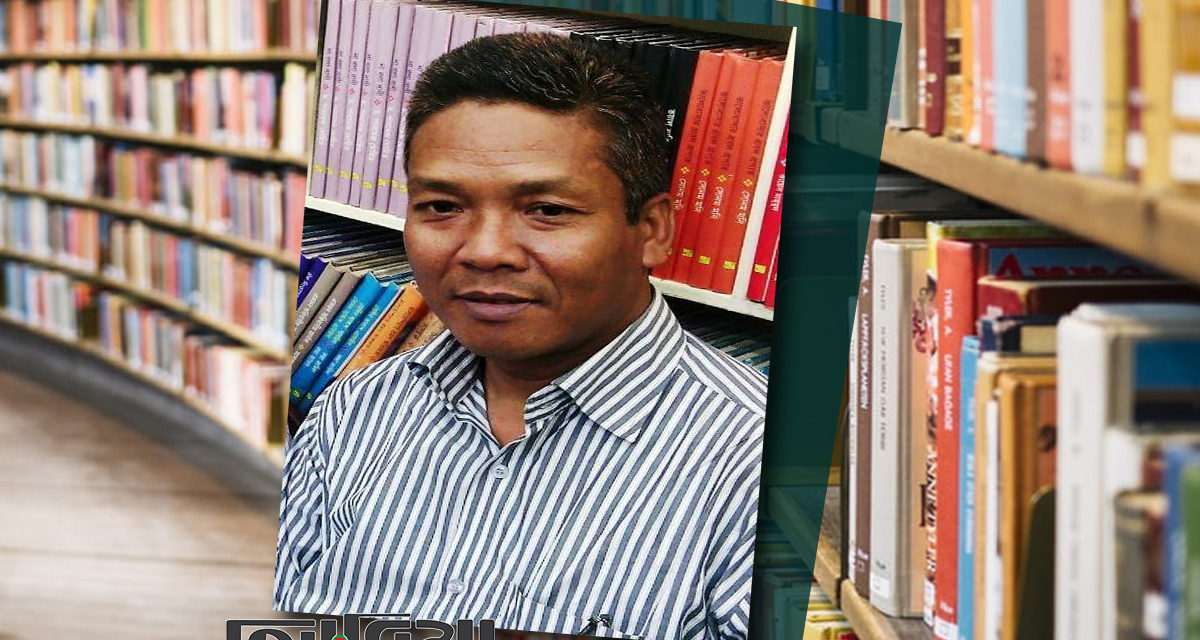বন্ধুবর লেখক ফিডেল ডি সাংমার জন্মদিনে লেখাটি উৎসর্গ করছি এবং তাঁর জীবন দীর্ঘায়ু কামনা করি। ফিডেল ডি সাংমা ছোটবেলা থেকেই ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ লেখার চর্চা করেন। একক প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ‘মিতা’এবং কাব্যগ্রন্থ ‘বন শালিকের অশ্রুবিন্দু’। এছাড়াও আদিবাসী কাব্য সংকলন ‘হাজলং’, এপার-ওপার বাংলার চল্লিশজন কবির কবিতা সংকলন ‘খুঁজি ফিরি তোমাকেই’ এবং হিমেল বরকত সম্পাদিত ‘আদিবাসী কাব্য সংগ্রহ’ নামক গ্রন্থে কবিতা সংকলিত হয়েছে। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ‘আর্চ বিশপ টি এ গাঙ্গুলি স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ গারো লেখক, গবেষক সম্মেলনে গল্পকার হিসাবে পুরষ্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।
বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের প্রতিটি মানবগোষ্ঠি সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, মেধা, মননশীলতা, সহজাত উপলব্ধি প্রভৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য লিপিবদ্ধ রেখে যেতে প্রয়াসী, উদ্যোগী হয়েছে; যা নি:সন্দেহে প্রতিটি জাতি, রাষ্ট্র তথা সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ, মানব জাতির জন্যে মূলবান দলিল। যখন থেকে বিভিন্ন বর্ণমালার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে; ঠিক তখন থেকেই এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই ধারা আরও বিষ্ময়কর, ব্যাপকতা, সুবিস্তার লাভ করছে দিনকে দিন। আজ আমরা দেখতে পাই সমগ্র বিশ্বে বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে লেখনী এবং এর বিকাশ সাধন করা।
বিশ্বের মোট জনসংখ্যার বিচারে গারোরা এক নগন্য জনগোষ্ঠি। কিন্ত বিভিন্ন ইতিহাস থেকে তাঁদের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস সুপ্রাচীণ ছিলো বলে জানা যায়, বিশেষ করে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে। আনুমানিক সাত হাজার বছর আগে তাঁদের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন এবং উত্তর ভারতে আর্য্যদের আগমন ও আর্য্য সভ্যতার বিকাশের অনেক আগেই গারোরা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলো। যার প্রমাণ হিসেবে আমরা পাই আর্য্য সভ্যতার প্রামাণিক মাহকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে গারোদের উপস্থিতির মাধ্যমে। এই দুটি মাহাকাব্যে গারোরা পরিচিত কিরাত জনজাতি নামে এবং সে সময় তাঁরা ছিলো অত্যন্ত সুসংবদ্ধ যোদ্ধা জাতি। কথিত আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদল গারো যুবক তৎকালীন কামরুপের রাজ্য ভগদত্তের সঙ্গে কৌরবদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলো। গারো যুবকদের এই দলটি যদি কৌরবপক্ষে অংশ গ্রহণ না করে পা-বপক্ষে অংশ গ্রহণ করতো তাহলে হয়তো আরো বিস্তারিত তথ্য জানা যেতো। কৌরব পক্ষের গ্লানিময় পরাজয়ের ফলেই গারো যোদ্ধাদের তেমন কোনো বিবরণ সুবিস্তারে পাওয়া যায় নি।
এইসব আদি কাহিনীসহ গারো গল্পকাররা সুবিন্যস্তভাবে তাঁদের উত্তর পুরুষের জন্য রেখে গেছেন যা আবহমানকালব্যাপী গারোদের মনে যুগপৎভাবে গর্ব, সাহস, আনন্দ, প্রেরণা প্রভৃতি যুগিয়ে আসছে অধ্যাবধি। যদিও সেগুলো অলিখিত পান্ডুলিপি বলা যায়, কিন্তু অপাংক্তেয় নয়; বরং গারোদের জাতীয় জীবনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে।
কিন্ত চরম দুর্ভাগ্য এবং বেদনার কথা হলো, গারো ভাষার প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে কথিত আছে, তিব্বত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকালে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বর্ণমালার জিম্মাদার লোকটি নাকি বর্ণমালা সম্বলিত পশুচর্মটি সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলে এবং ব্যাপরটি বেমালুম চেপে যায়। এরপর এদেশে আগমনের পর বহু প্রবীণ গারো সদস্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন যাদের সবাই ছিলেন গারো বর্ণমালা বিশারদ। ফলে তাঁদের মৃত্যুবরণের সঙ্গে সঙ্গে গারো বর্ণমালারও বিলুপ্তি ঘটে। যার পরিণামে বর্ণমালার অভাবে গারোদের মধ্যে অলিখিত মৌখিক সাহিত্য বেশ প্রভাব বিস্তার করে যা মূলতঃ লোককাহিনী হিসেবে পরিচিত।
গারো লোককাহিনী প্রধানত; তাদের নতুন দেশে অভিযান, রাজ্যজয়, বীরত্ব গাথা, নানা গোত্র-উপগোত্রের উদ্ভব ইত্যাদি কেন্দ্রিক এবং পাশাপাশি রয়েছে প্রেম বিরহের নানাবিধ কাহিনী যা গারোদের সামাজিক জীবনে এক শ্বাশত স্থান দখল করে আছে যুগের পর যুগ। এখানে এ জাতীয় দুটি প্রেম কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; প্রথমটি হচ্ছে ‘সেরেনজিং-ওয়ালজাং’ এর অমর প্রেম গাথা, আর দ্বিতীয়টি হল ‘আনাল-গোনাল’ এর অতি প্রাকৃত কাহিনী। এ জাতীয় অসংখ্য লোক কাহিনীর মধ্যে গারোরা তাঁদের শেকড়ের সন্ধান খুঁজে পায়। এগুলো তাঁদের কাছে নিছক রুপকথার গল্প মনে হলেও; বরং সত্যিকারার্থে এগুলো তাঁদের নিকট হাজার বছরের অমূল্য সামাজিক ইতিহাস, যার সূচনাকাল অজ্ঞাত।
এরপর বহু শতাব্দী গত হয়ে গেছে, সারা বিশ্বের মানুষ নিজ নিজ প্রতিভাকে লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসরে জগত সংসারে তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছে। গারোরা ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত হয়েছে, ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং নিজ নিজ মেধা ও প্রতিভাকে আক্ষরিক রুপ দিতে প্রয়াসী হয়েছে, কিন্তু সেটি অন্য বর্ণমালার মাধ্যমে। এহেন বলতে দ্বিধা নেই, আসলে গারোরা যে দুটি বর্ণমালার সহায়তায় গোড়া থেকে অদ্যাবধি তাঁদের সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন সে দুটি ভাষা হচ্ছে বাংলা এবং রোমান বর্ণমালা বা অক্ষর।
আদি পর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে গারোদের এই সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় রেভাঃ থাংকান সাংমা Life of Christ এবং Mission Work নামে দুটি বই ইংরেজীতে লিখেন এবং বই দুটি মিশনারী মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় রেভাঃ রামখে ওয়াট্টে মোমিন ১৮৮৭খ্রী. বাংলা-গারো অভিধান সংকলন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রেভাঃ মোমিন ছিলেন সেই দুজনের একজন যাঁরা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গারোদের মধ্যে প্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, অপরজন ছিলেন তাঁরই আপন মামা রেভাঃ উমেদ ওয়াট্টে মোমিন। ঐ দশকেই মধুনাথ মোমিন The Mirror of Heart নামে একটি অনুবাদগ্রন্থ সংকলন করেন। পরবর্তীতে দেখতে পাই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কাল মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গারো লেখক লেখিকা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যাদের মধ্যে মধুনাথ মোমিন, উইলসন মারাক, কার্নেশ মারাক, জোবাং ডি মারাক, ম্যাকেনসন রংমুথু, হরেন্দ্র মারাক, দেওয়াসিং রংমুথু, স্যামসন রংমুথু, এভিলিন মারাক, সুধীন্দ্র মারাক, লেভিনসন সাংমা, বিমলিন মোমিন, নরওয়েন মোমিন, জ্যাকসন মোমিন, রেভাঃ গিলবার্ট মারাক প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের অধিকাংশই ধর্মপুস্তক রচনা করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু দেওয়ান সিং রংমুথু, যিনি গারো লোক-কাহিনী সংগ্রহ এবং সংকলনের গুরু দায়িত্ব আজীবন পালন করে গেছেন, যে লোককাহিনীগুলোকে গারোদের সামাজিক ইতিহাস হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করা যায় আর একই সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ যাবত উপরোক্ত লেখকবৃন্দের লেখা প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন- Garo History, History of Assam, History of India, Itihasni Katharang, Life of Rev. Ramkhe Momin, Garo Folklore, Apako Gisik Raani, Apasong Agana, Folklores of the Garos, Achik Golporang, Achik Agana Bewalrang, Gitanjali, Arabian Walrang ইত্যাদি।
সাম্প্রতিককালে আমরা বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ গারো শিক্ষাবিদকে লেখক হিসেবে দেখতে পাই, যাঁদের মধ্যে ডঃ মিল্টন সাংমা (History and Culture of the Garos, Hill Societies, History of American Mission in North East India), ডঃ জুলিয়াস মারাক (Garo Customary Law and Practices, Balpakram-the Land of Spirit), মিহির এন সাংমা (Serenjing Waljang, Treaty between the British Government and Sonarm Sangma) প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে আসবে। এঁরা তিনজনই গারোদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকাচার প্রভৃতির উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এঁদেরকে অনায়াসে প্রথম সারির নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
প্রসঙ্গক্রমে যে কারণে গারো লেখিয়েদের ইতিহাস বলছিলাম, আর সেটি হলো- প্রত্যেক সৃষ্টিরভাজে মন্ত্রমুগ্ধ পেছন ইতিহাস লুকায়িত থাকে। তেমনি লেখকদের লেখার অন্তরালে থাকে কিছু পেছন স্মৃতি, থাকে আবছায়া প্রভাব, কারোর দিব্য, অগনিত অনুপ্রেরণা ইত্যাদি। দ্রুব সত্য কথাটি স্বীকার করি কিংবা নাই করি, এই সার্বিক এবং মৌলিক উপসর্গ উপস্থিত না থাকলে লেখকের লেখা হয়ে উঠে না।
পৃথিবীতে অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, নাট্যকার, কন্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার আছে যাঁরা জগতে সুখ্যাতির বাসনায় লিখে না। শুধুমাত্র নিজ আত্মতৃপ্তির নির্মিত্তে দুকলম লিখে, অনুশীলন করে থাকে। এভাবে লিখতে লিখতে-ই লেখক আবিস্কার করে ফেলে নিজেকে। আবিস্কার করে তাঁর লেখক সত্তাকে। এভাবেই দিব্যি লেখার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি পরিনত হতে থাকে একজন অদম্য জ্ঞান পিপাষু। শুরু হয় তাঁর সংস্কৃতিঙ্গানে সুদীর্ঘ পথ চলা। লেখকের হৃদয় নিংড়ানো আকাঙ্খা, বাসনা, দায়বদ্ধতা উপলব্ধি থেকে লেখকরা ধীরে ধীরে অনুভূতি প্রবণ হয়ে উঠে। হাতেখড়ি থেকে কেউবা কাব্যবুদ্ধা, খ্যাতিমান নাট্যকার, গল্পকার, নামজাদা লেখক, সাহিত্যিক, কন্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার হয়ে উঠে। তাঁর জীবদ্দশায় একজন সংস্কৃতি ধ্যানে জ্ঞানে অনিবন্ধিত এবং নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠে।
লেখকের মগজ ও ভাবনা জগতকে পূর্বাকাশে কালো মেঘের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কল্পিত করা যেতে পারে, ঝড় বৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃতিগতভাবে আকাশ এবং বায়ুমন্ডল কিভাবে যুগসূত্র হয়; কিভাবে প্রাকৃতিকভাবে একেওপরের সঙ্গে মিলন ঘটে। এসব ক্রিয়া-পক্রিয়া শেষ হলে আপনার মনে হবে এই বুঝি বৃষ্টি নেমে এলো ধরণীতে। সময় অসময়ে এমনই এক পরিস্থিতি এবং অদৃশ্য ভাবনা লেখকের হৃদয় গভীরে তোলপাড় করে। এমতাবস্থায় লেখক খাতা কলম নিয়ে প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে উঠে। শিশুটি মাতৃকোলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করে না। একেই বলে মেধাবৃত্তি এবং মেধাবৃত্তির চর্চা। তিনি ঘরোয়া, লোকারণ্যে ওফেনসিভ এবং অবিরত লিখে যান। আর সেটিই হলো লেখকের উপহার প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, নাটক, উপন্যাস, গ্রন্থ, গীত ইত্যাদি।
লিখতে লিখতে-ই লেখক; অতি দ্রুব সত্য কথা। ভালো লেখক হয়ে উঠা আরেকটি আপেক্ষিক প্রসঙ্গ। লেখক হতে চাইলে লেখক হওয়া যায় কথাটা অনেক বেশি সত্যি আর বাস্তব। প্রথম ইচ্ছেটাই সবার থেকে আলাদা একটা অনুভুতি এনে দেয় যে, আমি একজন লেখক হবো। এর সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। কিন্তু অনেকে-ই পারে না তাঁদের এই স্বপ্ন বা ইচ্ছাটাকে শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ দিতে। অবশ্য না পারার পেছনে যথেষ্ট কারন থাকতে পারে। আপনি তাহলে কিভাবে লেখক, ভালো লেখক হবেন সেই প্রশ্নটা এখানে আজ উহ্য থেকে যাক।
প্রবন্ধ লেখার প্রারম্ভে প্রসঙ্গত আরও বলছিলাম, গারোদের লেখকদের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার কথা। এই অভিযাত্রা থেমে নেই; এই পথে তাঁরা চলছে, অবিরত চলবে ভবিষ্যতেও। বর্তমান সময়ে গারো লেখকদের লেখনী ও বিভিন্ন সময় গ্রন্থ প্রকাশের তালিকার (লেখক/লেখিকা) বহর দেখে রীতিমতো বিস্মিত; তবে লেখার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি নি বরং আরও উৎসাহিতবোধ করি। কারণ কিছু কিছু লেখকদের বর্ণাঢ্য জীবনী থাকে; কিন্ত বাংলাদেশী ও ভারতের গারো লেখকেদের জীবনীতে তা সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। তাঁদের জীবদ্দশায় অথবা পূর্বে কেউ জাত লেখক, ভাবুক ছিল বলেও জানা যায় নি। নিজ আত্মপোলব্ধির মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে উঠে আসা। ফলে তাঁরা অকুতোভয় এবং নির্ভীক এক সাংস্কৃতিক কর্মী। এভাবেই তাঁদের জ্ঞানচর্চা এবং প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা; সংস্কৃতিক যাকযজ্ঞে এঁদের বিচরণ।
সাম্প্রতিক গারোদের শিক্ষার হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষার হার বেড়েছে ঠিকই; কিন্ত সে হারে লেখালেখির পরিবেশ তৈরী হয় নি। লেখক তৈরীর বৈরি পরিবেশ হলেও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যাঁরাও লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃত্ত তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন-জীবিকার দরুন লিখন শিল্পকে শতভাগ পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারে নি। জাতীয় পর্যায়ে লেখক, পেশাদার লেখক হয়ে উঠতে পারে নি। মোদ্দা কথা, আত্মনির্ভরশীল, প্রতিষ্ঠিত এমন লেখক এখনো হয়ে উঠতে পারে নি। হয়ে না উঠার পেছনে কারনও অনেক রয়েছে। অনেকগুলো কারনের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দুটোকেই বেশি দায়ী করা যেতে পারে; বাকী কারণগুলো অবশ্য আপেক্ষিক।
বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পটি এখনো নানা ভেড়াজালে আবদ্ধ, ঝড়াজীর্ণ অবস্থা। সংস্কারের উদ্যোগ চোখে পড়ে নি এখনো। অর্থাৎ এই জ্ঞান বা মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রটি নিখুঁত নয়; ফলে শিল্প সাহিত্যের বাজারে রাজনীতি, ব্যবসা ওতোপ্রতভাবে প্রবাহমান। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে শিক্ষিত গারো সমাজে সাহিত্য চর্চায় গতিশীলতা প্রত্যাশিত ছিলো বটে, তবে সেটি আজও পূরণ হয় নি। গারো লেখকরা দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে শিল্পটি চর্চা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। যার ফলে এই দ্বিতীয় ভাষার ওপর তাঁদের দখল কেমন সেটিও ভাবার এবং দেখার বিষয়। এতকিছুর পরও আরও বড় সমস্যা হচ্ছে; গ্রন্থ প্রকাশে পৃষ্টপোষকতা, যোগাযোগ, প্রচারণা ইত্যাদিতেও তাঁরা সুবিধা বঞ্চিত এবং অবহেলিত।
কিছু কিছু গারো লেখকদের লেখার মান উঁচু দরের না হলেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির লেখকদের লেখনীর তুলনায় একেবারে ফেলনাও নয়। পেশাদার লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এমন লেখক আমাদের মধ্যেই আছে। কিন্তু সে স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেছে। প্রকাশনা শিল্পে পৃষ্টপোষকতার অভাবে নিজ খরচে এবং বহু কষ্টে বই মেলায় বই ছাপিয়ে যাচ্ছেন; তবে দুয়েকজন ছাড়া। নিজ খরচে বই ছাপতে গিয়ে বেগ পোহাতে হয়, চরম নাজেহাল হতে দেখা গেছে লেখকদের। আদিবাসী লেখক হলে তো আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশে গারো লেখকদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ কী নেই! বই মেলাকে পূঁজি করে গারো লেখক, কবিরাও নিজেদের প্রচার প্রসারে স্থান করে নিতে চান। প্রতিযোগিতা জগতে টিকে থাকতে চায় তাঁদের মেধা মনন দিয়ে। যুগে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে উঠতে চায় এমন অনেকে-ই। তাঁরা হয়ে উঠতে চায় জাতীয়, আন্তজার্তিক মানের প্রতিষ্ঠিত লেখক।
আমাদের সমাজে এমন কেউ কেউ আছে অর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা লেখক হিসেবে না হোক, অন্তত একজন ভালোমানের পৃষ্টপোষক, প্রকাশক হতে পারতো। এই প্রকাশনা শিল্পকে পূঁজি করে অনেক সাহসী ব্যক্তি পূঁজিবাদিতে পরিনত হয়েছে। পূঁজি বাজারে তাঁদের দাপত লক্ষ্য করার মতো বিষয়। আগামী দিনগুলোতে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ লেখক, পৃষ্টপোষক, প্রকাশক হয়ে উঠবে যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটিকে আজকে গারো নতুন প্রজন্ম এবং যুগের দাবী বলা-ই সমীচিন।
গারো শিল্প সাহিত্যের দলিল এবং পরবর্তী প্রজন্মদের কথা চিন্তা করে কিছু তরুণ উদ্যোক্তা, ব্যক্তি উদ্যোগে গারোদের প্রকাশনী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে বলে বিভিন্ন মাধ্যম হতে জানতে পেরেছি। এ পদযাত্রা শুধু আশার কথায় নয়; এই ধরণের উদ্যোগ প্রকাশনীতে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামনের দিকে নীরবিছিন্নভাবে এবং আলোর পথে এগুতে পারলে গারো লেখকদের সংস্কৃতি, সাহিত্য চর্চার দায় কিছুটা হলেও ঘুচবে।
লুই সাংমা, ফ্রান্স
ওয়েভ ডেভেলপার, ব্লগার, আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্সার এবং
সাংস্কৃতিক কর্মী।
তথ্যসূত্র :
সুভাষ জেংচাম, গারোদের সাহিত্য চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।