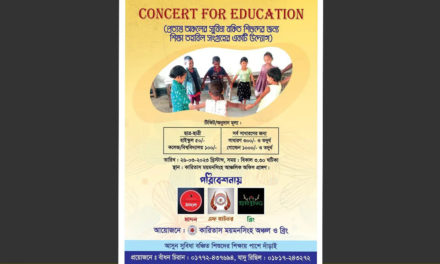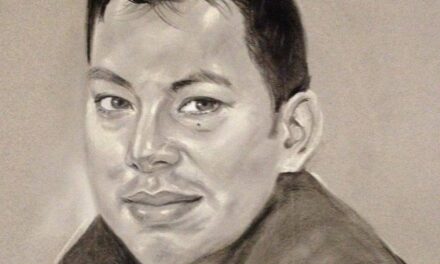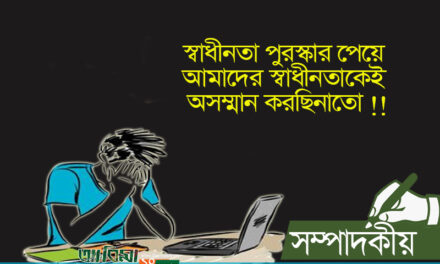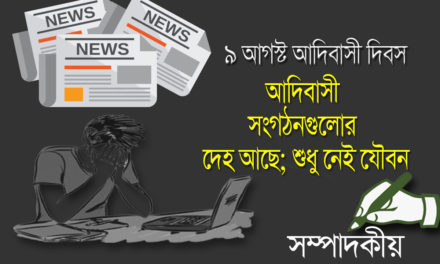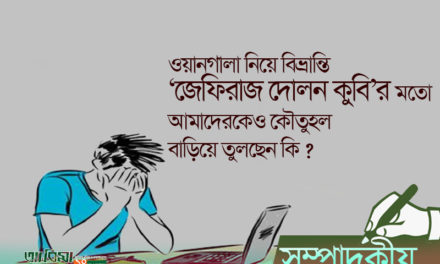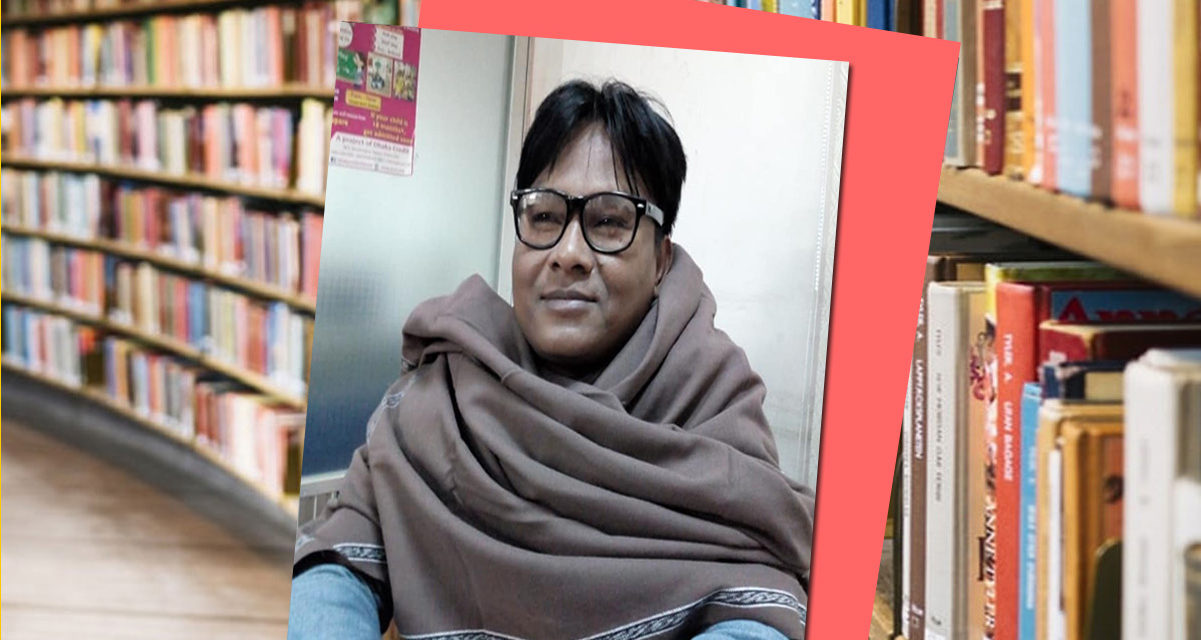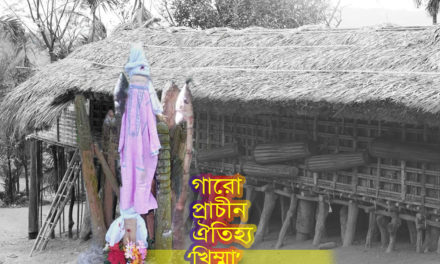এ বিষয় নিয়ে লেখার কোন প্রয়োজন আছে এরকম মনে না হলেও দিব্যি লিখতে বসে গেছি। শুরুও করছি। কেন লিখছি, লিখতে শুরু করেছি, এর কোন সুস্পষ্ট হেতু আমার জানা নাই। আর এ বিষয় যে আমার চেতন ও অবচেতনে এসে যাচ্ছে এমনও না। প্রকৃতপক্ষে এটা এক মামুলি বিষয়ই- আমার কাছে, আমাদের কাছে, এবং সবার কাছে।
জিকপাংমা এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আর এটা নিয়ে লেখার কোন অভিপ্রায় আমার ভেতরে ছিল না।
এ তো সবারই জানা কথা, ইতোপূর্বে পাণিগ্রহণ না করা কোন যুবক-যুবতী বা পুরুষ-মহিলা যখন সংসার শুরু করে, সে নকনা কন্যাই হোক কিংবা আগাতি-সে-ই সেই সংসারের জিকপাংমা হয়। এ জিকপাংমাই ওই সংসারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়। এটাই যুগে যুগে, কালে কালে, বংশ পরম্পরায় গারোদের পালনীয় বেওয়াল, পালনীয় রীতি। এখানে সুনির্দিষ্ট অর্থে ‘বেওয়াল’মানে গারোদের পালনীয় সমাজ ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি, প্রথা, শাসন-অনুশাসন ও জীবনাচার। এবং নকনা’র এক ও অদ্বিতীয় উৎস এ জিকপাংমাই।
গারো সমাজে এ ‘জিক’বা ‘স্ত্রী’হয় তিন ধরনের। এক জিকপাংমা (প্রথম স্ত্রী)। দুই জিকগিদি (দ্বিতীয় স্ত্রী)— ইনি জিকপাংমা থাকা অবস্থায় বা না-থাকা অবস্থায় মৃত্যুর পর জিকগিদি হয়ে আসতে পারে (জিকগিদিও প্রথম জিকগিদি, দ্বিতীয় জিকগিদি এভাবে আরও হতে পারে )। তিন জিকব্রিং—ইনি লোক মুখে চাউর থাকে, সে তো বা অমোক তো অমোকের জিকব্রিং। কিন্তু কেউ তাকে তার জিক বা স্ত্রী হিসেবে স্বিকৃতি দেবে না, স্বীকার করবে না। কিংবা জিকব্রিং নিজেও স্বীকার বা অন্যদের বলবে না আমি অমোকের জিক। বললে চরিত্রের কলুষতা ও কলঙ্কের কালিমা প্রকাশ্য হয়। ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য হতে হয়। বাস্তবিকও তার সাথে পুরুষের যে সম্পর্ক সেটা গোপনের, লোকচক্ষুর অন্তরালের। সমাজ ও পরিবারের অজ্ঞাতে হয়। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে এর কোন স্বীকৃতি নেই।
জিকব্রিং শব্দটি ব্যবচ্ছেদ করলেও এরকম হয় ‘জিক’মানে স্ত্রী, ‘ব্রিং’মানে জঙ্গল। মানে এ সম্পর্ক লোকসমাজের ভেতরের মধ্যের নয়, বাইরের।
লেখাটিকে আরও সুস্পষ্ট করতে গারোদের বেওয়ালে জামাই দু’ধরনের হয়- এক) নক্রম, দুই) চাওয়ারি; এটিও বলা প্রয়োজন। আর এ জামাই সে ‘নক্রম’ই হোক, কিংবা ‘চাওয়ারি’তাকে তার স্ত্রীর গৃহে আসতে হয়, থাকতে হয়, বসবাস করতে হয়। আর এ ‘নক্রম’ও ‘চাওয়ারি’র মধ্যে রয়েছে অধিকার, ক্ষমতাকাঠামো ও সামাজিক মর্যাদাগত পার্থক্য। এখানে ‘নক্রম’হলো কোন পরিবারের ‘নকনা’মনোনীতা কন্যার জামাই, আর ‘চাওয়ারি’হলো নকনা ব্যতীত অন্যান্য ‘আগাতি’কন্যা সন্তানদের জামাই। বেওয়াল অনুযায়ী নকনা-নক্রম পিতা-মাতার সাথে একই পরিবারভুক্ত হয়ে সংসার জীবন করে কিন্তু আগাতি ও চাওয়ারিদের কিছুদিন পিতা-মাতার সংসারে থেকে আলাদা ঘর সংসার করতে হয়।
আর বংশ গণনায় গারোরা পুরুষ বা পিতার দিক থেকে করে না মাতার দিক থেকে করে। পরিবারের সন্তান-সন্তুটিরা বংশধরেরা মাতার চাৎচি মাহারি বা পদবী গ্রহণ করে পরিচিত হয়। এর কোনরূপ ব্যতয় গারো সমাজে অচিন্ত্যনীয়। সেরকম হলে গারোরা সেটাকে পাপ কর্মের চেয়েও ঘৃণীত ও তিরস্কৃত জ্ঞান করে। সর্বাবস্থায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র-পাত্রি করে।
আর মেয়ে সে নকনাই হোক, কিংবা আগাতি প্রথম স্ত্রী গারো সমাজে ‘জিকপাংমা’ হিসেবে পরিচিত হয়। আর এ জিকপাংমাই ওই পরিবারের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়। আর ওই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরসূরী উত্তরাধিকারিণী হয়- পরিবারে যদি একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে নকনা মনোনীতা কন্যা সন্তান, আর একমাত্র কন্যা সন্তান থাকলে সেই উত্তরাধিকারিণী হয়। আর যদি কোন কন্যা সন্তানই না থাকে তবে চ্রা-চাৎচিদের অনুমতিক্রমে জিকপাংমা নিজের পছন্দানুযায়ী নিজের সহোদরা ও আপন নিকটতম বোনদের যেকোন কন্যা সন্তানকে কন্যা ও কন্যার মা-বাবার সম্মতিক্রমে নকনা মনোনীতা করতে পারে। এও যদি সম্ভব না হয়, বা, বোনদেরও যদি কন্যা সন্তান না থাকে তবে একই মাহারির দূর সম্পর্কের বোনদের কন্যা সন্তানদের নকনা হিসেবে মনোনীতা করবে। এক্ষেত্রে এ নকনা মনোনীতা কন্যা নিজের আপন মা-বাবা, ভাই-বোনদের রাগ-অনুরাগ বিযুক্ত থেকে ও তাদের প্রতি দায় রহিত থেকে এ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং সেই এ জিকপাংমা ও তার স্বামীকে আমৃত্যু লালন-পালন করবে, এ পরিবারের ভাই বা চ্রাদের বিপদ-আপদের বৈধ জামিনদার হবে। গারোরা এভাবে নকনা মনোনয়ন করাকে ‘নকনা সৎদে রাবা’বলে। এখানে ‘সৎদে’মানে কাটা, আর ‘রাবা’মানে আনা। ‘সৎদে রাবা’মানে ‘কেটে আনা’। তবে একাধিক স্ত্রী থাকলে, জিকগিদি যদি একই মাহারির হয় এবং এ জিকগিদির যদি কন্যা সন্তান থাকে তবে সে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নকনা’র অধিকার লাভ করবে। এ ব্যতিরেকে ওই পরিবারে জিকগিদি ও জিকগিদির সন্তানদের সম্পত্তি প্রাপ্তির কোন অধিকার নেই। যদি নকনা তাদের দেয় তবে তারা সেটা নিয়েই সন্তোষ্ট থাকবে।
এ জিকপাংমা (জিক + পাং + আমা) শব্দের ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ‘জিক’ মানে স্ত্রী, ‘পাং’মানে গাছ, ‘আমা’ মানে মাতা। অর্থাৎ কোন গারো পরিবারে জিকপাংমা হলো ওই পরিবারের মূল বা শেকড়। এটাই গারো সমাজের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অলঙ্গনীয় মান্য রীতি।
বেওয়াল অনুযায়ী পারিবারের নকনা কন্যা সন্তানদের জন্য নক্রম কারা হয়, হতে পারে, বাস্তবে এ মৌলিক ও যৌক্তিক সুন্দর রীতি এখন সর্বাংশে মানা না হলেও বেওয়াল অনুযায়ী পুরুষের বা ওই পরিবারের কর্তার ওপর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের যে দায়িত্ব অর্পিত থাকে তা যুগ-যুগান্তরে পুরুষানুক্রমে কর্তার বা পিতার চাৎচি মাহারি বা পিতার বংশের ওপরই যাতে বর্তায়, যাতে অন্য মাহারির পুরুষের তত্ত্বাবধানে চলে না যায়, এ কারণে কর্তার বা পিতার আপন ও নিকটতম ভাগ্নেয়, না থাকলে দূর সম্পর্কের (একই মাহারির) ভাগ্নেয়কে নকনার নক্রম করে আনা হয়। দূর সম্পর্কের ভাগ্নেয়কে নক্রম করে আনাকে গারোরা ‘নক্রম সৎদে রাবা’বলে। একইভাবে আগাতি কন্যা সন্তানদের জন্যও প্রথমে পিতার চাৎচি মাহারির ভাগ্নেয়দের চাওয়ারি হিসেবে দেখা হয়, না হলে অন্য চাৎচি মাহারি থেকে দেখা হয়। আগাতি কন্যা সন্তানদের পিতার চাৎচি মাহারিকেই বিয়ে করতে হবে, বা, পিতা-মাতা পছন্দ করা পাত্রকেই বিয়ে করতে হবে এ বাধ্যবাধকতা নেই।