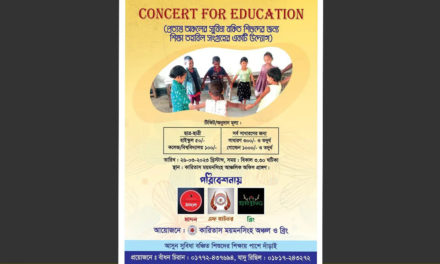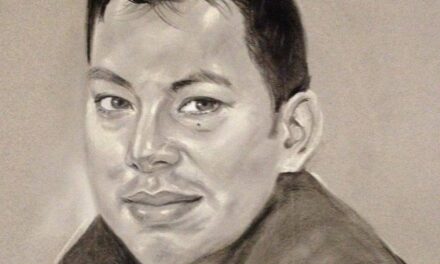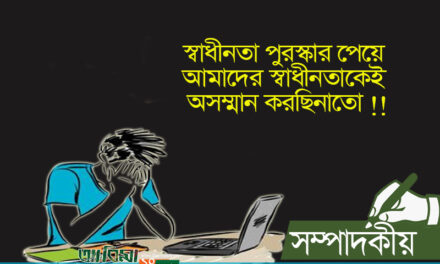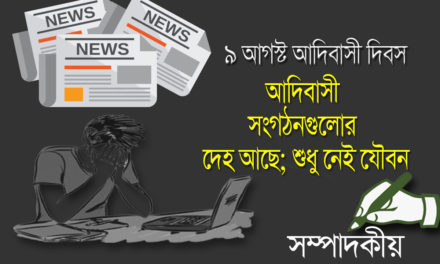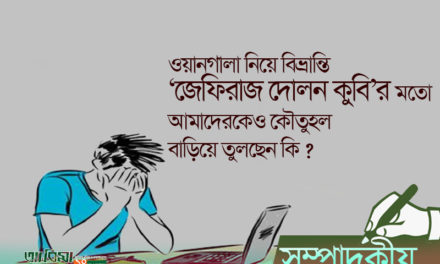আদিবাসী বিষয়ে জাতিসংঘ এবং এর অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি চার্টারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে- ১৯৫৭ সালের ৫ জুন অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৪০তম অধিবেশনে প্রদত্ত- Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), আইএলও’র ১৯৮৯ সালের ৭ জুন অনুষ্ঠিত ৭৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), এবং ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ৬১তম অধিবেশনে The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
আইএলও’র প্রথম চার্টার দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, চার্টার দুটির শিরোনাম হচ্ছে- Indigenous and Tribal Populations Convention. অর্থাৎ আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন। অর্থাৎ এই কনভেনশনটি আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। কনভেনশনে পাস হওয়া ধারাগুলো একই সাথে আদিবাসী ও উপজাতি নির্ধারণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
এখানে উপজাতি ও আদিবাসীদের জন্য আলাদা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)– এর আর্টিকল ১ এর (a)তে ট্রাইবাল বা উপজাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ‘tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations’. অর্থাৎ একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্নতর যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও আইন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত তাদেরকে উপজাতি বলা হয়।
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)–এর আর্টিকল ১-এর (b)তে ইনডিডজিন্যাস বা আদিবাসীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ‘Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions’. অর্থাৎ আদিবাসী তারা যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত হওয়া ও উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করছে। এবং যারা তাদের কিছু বা সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে।
বিভিন্ন জড়িপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য হচ্ছে- বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি জাতিসত্ত্বার উপস্থিতি রয়েছে; যাদের জাতিগোষ্ঠির প্রত্যেকের জীবনধারা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিসমূহে ভিন্নতা রয়েছে এবং তা বৈচিত্রপূর্ণ। বাংলাদেশে ‘এথনোগ্রাফিয় গবেষণা’ নামে একটি গবেষণা চালিয়ে তা তিনটি খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম খন্ডে যে জাতিগোষ্ঠি রয়েছে যেমন- অহমিয়া, খিয়াং, খুমী, গুর্খা, চাক, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, বম, মারমা, ম্রো ও লুসাই। দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে- কোচ, খাড়িয়া, গারো, ডালু, বানাই, হাজং, খাসিয়া, পাত্র, মণিপুরি ও রাখাইন। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে- ওরাওঁ, কন্দ, কোল, গন্ড, তুরি, পাহান, পাহাড়িয়া, বাগদি, বেদিয়া, ভূমিজ, মাহাতো, মাহালি, মালো, মুন্ডা, মুরাবী, মুষহর, রাই, রাউতিয়া, রাজোয়াড় ও সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠি। এই গ্রন্থ এবং সমীক্ষাটিই প্রমান করে বাংলাদেশে আদিবাসীদের অস্থিত্ব আছে, তাঁদের জীবন জীবিকা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য একেবারেই আলাদা। ফলে বর্ণাঢ্য জাতিগোষ্ঠির সহাবস্থান এ দেশকে দিয়েছে বিশেষ মাত্রা; বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।এ বৈচিত্রপূর্ণ সমাজ সংস্কৃতির কারণে দেশে এবং বিদেশে আদিবাসীদের টিকে থাকা, নিরাপত্তা, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহ এবং সহযোগিতা করতে দেখা গেছে। জাতিসংঘের আদিবাসী-বর্ষ ঘোষণার পর এই ৪৫টি জাতিগোষ্ঠি নিয়ে বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলন ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠিত হয়।
নৃ-তাত্ত্বিকরা বলেন, আদিবাসি/উপজাতীয় সংস্কৃতি প্রধানত ধর্ম থেকে উৎসারিত। কিন্তু বাংলাদেশের আদিবাসি/উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী গড়ে ৯০ ভাগ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম এবং কিছু অংশ মুসলিম এবং হিন্দু গ্রহণ করেছে। মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যেও প্রায় ৫০ ভাগ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। চাকমাদের ক্ষেত্রে এই হার কিছুটা কম। কিন্তু চাকমাদের আদি ধর্ম বৌদ্ধ নয়। ব্রিটিশ আমলে রানী কালিন্দী রায়ের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার আগে চাকমা রাজারা মুসলমান ছিল। মোগল আমলের পূর্বে তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করতো। এভাবে ধর্ম পরিবর্তনের সাথে সাথে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার, রীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির প্রভাবেও পাল্টে গেছে জীবনযাপনও। কয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া নাগরিক ও সচ্ছল আদিবাসি বা উপজাতিদের নিজস্ব পোশাকের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানকার মিশনারীরাও ধর্মান্তরিত উপজাতিদের পূজা-আচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে ‘আদিবাসী’ তকমা ধরে রাখার জন্য।
অন্যদিকে, রাজনৈতিক ইস্যূ, নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী ইস্তেহার কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বক্তৃতায়, মিডিয়ায় আদিবাসী শব্দের স্থলে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সরকার পক্ষের বক্তব্যগুলো শিরোনাম হয়ে উঠে আসে, প্রচার করা হয়- দেশে কোন আদিবাসী নেই। কনভেনশন ও চার্টার অনুযায়ী ট্রাইবাল বা উপজাতির যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা বিচার করেই নাকি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো উপজাতি বলা যায়। একই কারণে আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘ চাটার বাংলাদেশের উপজাতিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন মিডিয়াতে, কিছু বিজ্ঞজনের লেখনীতে উঠে আসে, বাংলাদেশে আদিবসী স্বার্থ বিষয়টি মিডিয়া এবং কিছু কিছু সুশীলদের একটি এক্সক্লোসিভ প্রচারণা বলে অভিযোগ করেন। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের আদিবাসীরা কোনভাবেই জাতি সংঘের প্রণিত আদিবাসীর সংজ্ঞায় পড়ে না। ফলে আদিবাসীদের অধিকার এবং তাদের স্বীকৃতি বিষয়টি এখন কোন কোন দলের রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বৈষম্যপূর্ণ, অসামঞ্জস্য ও পারস্পরিক স্ববিরোধী কার্যক্রম থেকে প্রতীয়মান হয় কী সত্যিই বাংলাদেশে কোন আদিবাসী জাতিসত্ত্বা নেই? নাকি আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বজ্ঞানে অস্বীকার করে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে শুধুমাত্র বাঙালী জাতিসত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলছে বলে বিষয়টি আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত শঙ্কার মধ্যে রয়েছে।
আদিবাসী বিষয়ক আভিধানিক শব্দ বা প্রতিশব্দগুলো ছাড়াও জাতিসংঘ প্রদত্ত আদিবাসী সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক উপজাতি ও আদিবাসী সংজ্ঞার মূল পার্থক্য হচ্ছে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বংশানুক্রমে বসবাস বা অধিকৃত হওয়ার বা উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে বসবাস করা বুঝায়। আদিবাসী ফোরাম এবং আমি ব্যক্তিগতভাবেও মনে করি- যে জনগোষ্ঠির নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আছে এবং একটি অঞ্চলে দীর্ঘকালের বর্ণাঢ্য ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে তাঁদের উপজাতি বলার চেয়ে আদিবাসী বলে অভিহিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত।